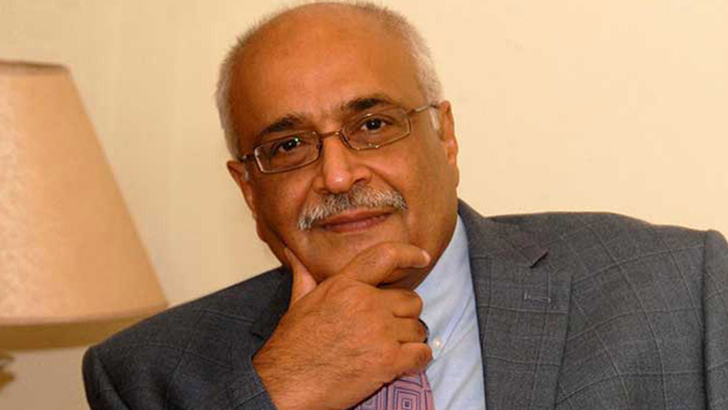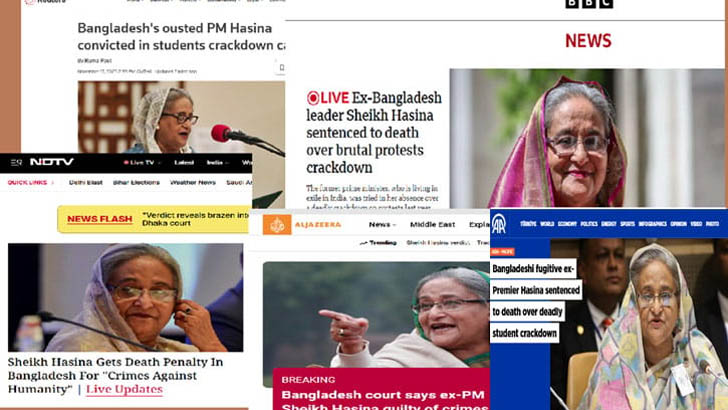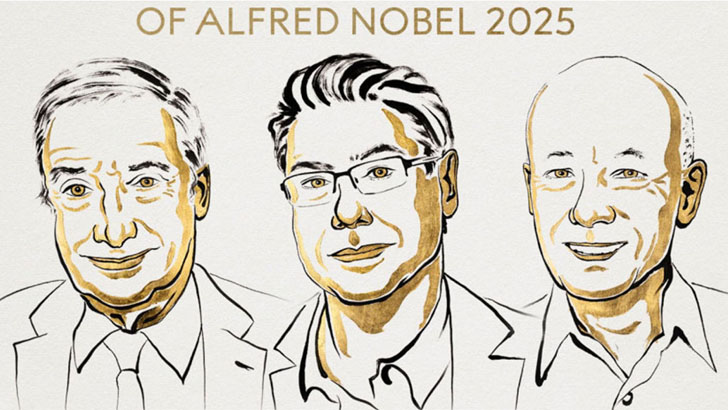বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নিয়ে মন্তব্য করার আগে ভারত সরকারের মনে রাখা উচিৎ যে, তাদের নিজ দেশে সংখ্যালঘুদের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়— তার একটা প্রভাব অবশ্যই পড়ে। ভারতের ফোর্টনাইটলি ম্যাগাজিনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে একথা বলেছেন বাংলাদেশের বরেণ্য এই বিশেষজ্ঞ।
সাক্ষাৎকারটি আজ মঙ্গলবার (১ এপ্রিল) তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। দেবপ্রিয়ের সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন ফোর্টনাইটলির নিরুপমা সুভ্রামনিয়ান। গত বছর আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর থেকে বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কসহ নানান বিষয়ে তাঁরা কথা বলেন।
সম্প্রতি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর দেশটির পার্লামেন্টে জানিয়েছেন, ২০২৪ সালে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর ২,৪০০ বার আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে, ২০২৫ সালে এ ধরনের ৭২টি ঘটনা ঘটেছে।
এ বিষয়ে ড. দেবপ্রিয়’র মন্তব্য জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, আমি মনে করি এসব সংখ্যা অতিরঞ্জিত। আর বিভিন্নভাবেই এ ধরনের হিসাব দেওয়া সম্ভব।
তিনি বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর দেশত্যাগের পর বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি হয়েছিল। ‘পুলিশ বাহিনী একটা ছত্রভঙ্গ অবস্থার মধ্যে ছিল। কিছু সময়ের জন্য, দেশের পুরো নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে হয় সেনা ও আধা-সামরিক বাহিনীকে, কিন্তু তবু পরিস্থিতি ছিল অস্থিতিশীল।
দেবপ্রিয় আরও বলেন, ‘বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অনেকেই ঐতিহাসিকভাবে সাবেক ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেছে। তাই কিছুক্ষেত্রে ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে কোনো হিন্দু ব্যক্তির ওপর হামলা করা হয়েছে, নাকি রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগের সমর্থক হওয়ায় হামলার ঘটনা ঘটেছে— তা আলাদা করে বলা কঠিন।
বাংলাদেশের অর্থনীতির শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রধান আরও উল্লেখ করেন যে, এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়কে বিবেচনায় নিতে হবে।
‘বাংলাদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধরা সংখ্যালঘু, আবার ভারতে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর অংশ। একইভাবে ভারতের মুসলমানরা সংখ্যালঘু, কিন্তু বাংলাদেশে সংখ্যগরিষ্ঠ। তাই ভারত যখন বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণ নিয়ে মন্তব্য করে, তখন তারও উচিৎ নিজ দেশের সংখ্যালঘুদের প্রতি করা আচরণের একটা প্রতিক্রিয়াও হবে।’
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন হিসেবে বাংলাদেশে তিনি কতোটা নিরাপদবোধ করেন, এমন প্রশ্ন করা হলে দেবপ্রিয় বলেন, ‘এক্ষেত্রে আমি হয়তো সবচেয়ে ভাল উদাহরণ হব না। ভারতে আমি দুইবার শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেই— একবার ১৯৬০’এর দশকের দাঙ্গার কারণে ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত, আরেকবার ৭১’ এর মুক্তিযুদ্ধের সময়। কিন্তু, আমার মা-বাবা কখনোই বাংলাদেশ ত্যাগ করেননি। আমিও দেশে ফিরে, মাতৃভূমির জন্য কাজ করেছি, সেখানে আমার জীবন গড়েছি। আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত পদ ছেড়ে— আমি দেশের জন্য অবদান রেখেছি।
তিনি আরও বলেন, তার পরিবারের বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও বিচারিক ইতিহাসের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রয়েছে।
‘আমার মা শেখ হাসিনার দলের [আওয়ামী লীগ] সংসদ সদস্য ছিলেন, আর বাবা ছিলেন— শেখ মুজিবুর রহমানের নিয়োগপ্রাপ্ত সুপ্রিম কোর্টের বিচারক। তবে এ পারিবারিক সম্পর্ক আমার পেশাদারিত্ব কিংবা তথ্যভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করে না,’ তিনি বলেন।
বাংলাদেশে পরিচয়ের রাজনীতি (আইডেনটিটি পলিটিক্স) যেভাবে ভূমিকা রাখে, তাতে কিছু ঝুঁকি রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, আমাদের সমাজের একটি বড় অংশ ধর্মনিরপেক্ষতা, মানবাধিকার ও সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুরক্ষার পক্ষে—হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগত সংখ্যালঘু কিংবা সমতলভূমির আদিবাসী গোষ্ঠী। এ অন্তর্ভুক্তির অঙ্গীকারই জাতি গঠনের মূল ভিত্তি।
সাক্ষাৎকারে সংবিধান থেকে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শব্দটি বাদ দেওয়া ও ‘বহুত্ববাদ’-এর সংযুক্তির জন্য সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্কের বিষয়টিও আলোচনায় আসে।
এবিষয়ে দেবপ্রিয় বলেন, এটি সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লিখিত একটি প্রস্তাবমাত্র, এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। ‘এটি একটি চলমান রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, যেখানে বিভিন্ন পক্ষের মতামত বিবেচনা করা হবে। তাই এ মুহূর্তে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখানো অপ্রয়োজনীয়, কারণ বিষয়টি এখনো পর্যালোচনার পর্যায়ে রয়েছে।
তিনি আরও বলেন, গণতান্ত্রিক সমাজে মতপার্থক্য থাকাটাই স্বাভাবিক, তবে কেউ কেউ অজ্ঞতা, আদর্শিক অবস্থান কিংবা রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে কট্টর মতামত প্রকাশ করেন।
‘…বাংলাদেশের কিছু মানুষ ইতিহাস পুনর্লিখন করতে চায়, তবে তাদের দর্শন জাতীয় নীতি নির্ধারণে প্রভাব ফেলবে, এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই,’ তিনি যোগ করেন।
সবুজদেশ/এসইউ


 সবুজদেশ ডেস্ক:
সবুজদেশ ডেস্ক: